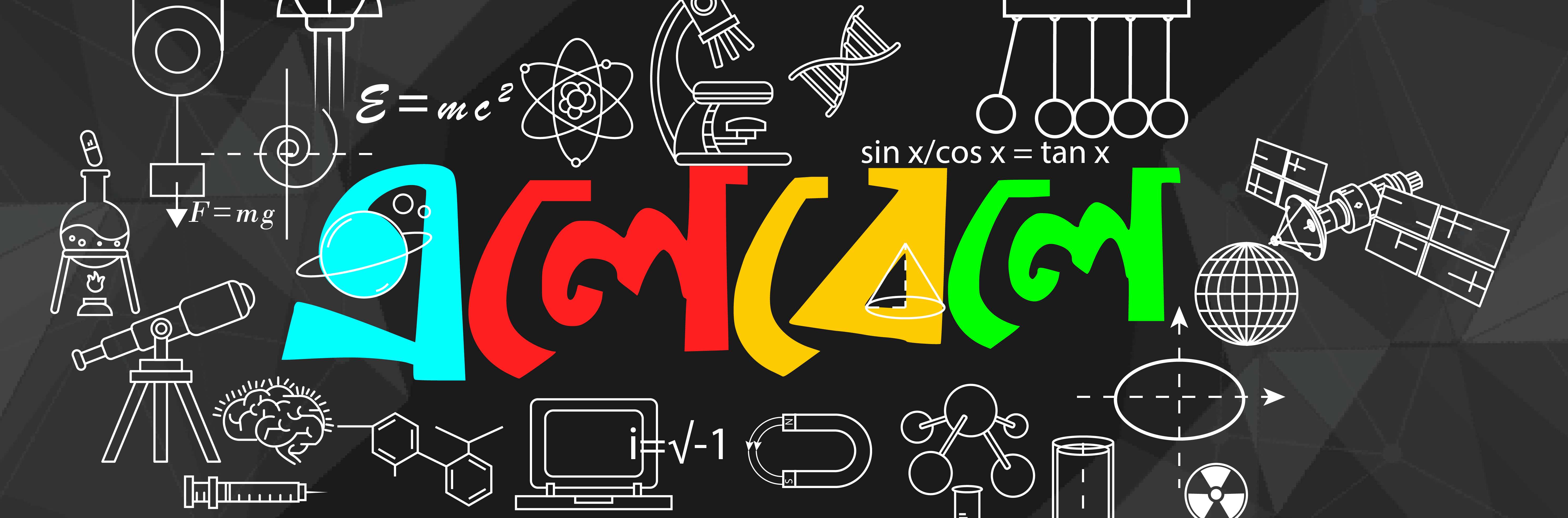~ কলমে এলেবেলে চিরশ্রী ~
১৯০০ সাল। জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটির (ডি.পি.জি.) এক সম্মেলনে নিজের সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রটি পড়ে শোনালেন পদার্থবিদ ম্যাক্স প্লাঙ্ক। বিজ্ঞানী মহল সেদিন খুব একটা পাত্তা না দিলেও সবার অলক্ষ্যে ঘটে গেল এক নিঃশব্দ বিপ্লব; জন্ম নিল পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন এক অধ্যায়। কি এমন ঘটেছিল সেদিন যা ভবিষ্যতে বিজ্ঞানচর্চার অনেক দরজা একসঙ্গে খুলে দিয়েছিল? সেটা বোঝার জন্য অবশ্য আমাদের আরও প্রায় দু’দশক অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে সেই গল্প শুরুর আগে আমাদের একবার অতীতে হেঁটে আসতে হবে। সময় যানে চড়ে প্রথমেই আমরা পৌঁছে যাব ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকটায়।
ততদিনে পদার্থবিদ্যার ঝুলিতে মজুত হয়ে গেছে তড়িচ্চুম্বক বিজ্ঞান, তাপ-গতিবিদ্যা এবং সনাতন বলবিদ্যার ধারণা। তড়িচ্চুম্বক বিজ্ঞানের শাখায় আমরা আলাপ করে ফেলেছি আলোর তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গধর্ম বা বিকিরণের সাথে। তাপ-গতিবিদ্যা শিখিয়েছে তাপের সঙ্গে অন্যান্য শক্তির (যেমন যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক বা রাসায়নিক শক্তি) সম্পর্ক। আর নিউটনের হাত ধরে সনাতন বলবিদ্যার জগতে তো সেই কবেই প্রবেশ করেছি, জেনেছি চারপাশের বস্তুজগতের গতিবিজ্ঞান। শুধু তাই নয়, তৎকালীন ধারণা আমাদের শিখিয়েছে বস্তু (বা কণা) এবং বিকিরণ (বা তরঙ্গ) আসলে দু’টি ভিন্ন সত্তা, যারা নানা (তাপ-গতিবিদ্যা ও তড়িচ্চুম্বক বিজ্ঞান) উপায়ে একে অপরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। মানুষ ভাবতে শুরু করেছে, বোধ হয় প্রকৃতির সমস্ত রহস্যই এখন তার হাতের মুঠোয়।
এরকম একটা সময়ে মিউনিখ ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা করছেন ছাত্র প্লাঙ্ক। একজন প্রতিভাবান ছাত্রের পদার্থবিদ্যায় এত আগ্রহ, অথচ তার নতুন কিই বা দেওয়ার আছে বিজ্ঞানকে? বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক পি. ভি. জোলি একদিন ছাত্র প্লাঙ্ককে ডেকে বলেই ফেললেন – এই শাখায় প্রায় সবকিছুই তো ইতিমধ্যে আবিষ্কার করা হয়ে গেছে, রয়ে গেছে শুধু কিছু ছোটখাটো ফাঁকফোকর। প্রত্যুত্তরে সেদিন সেই ছাত্র জানিয়েছিলেন – তিনি আদৌ নতুন কিছু করতে চান না, শুধু পদার্থবিদ্যার মূল তত্ত্বগুলো একটু ভালোভাবে জানতে চান। সেই জানার তাড়নাই ভবিষ্যতে প্লাঙ্ককে এনে দেবে কোয়ান্টামের দোরগোড়ায়, কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের (ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশন) হাত ধরে। তবে সেই দরজায় কড়া নাড়ার আগে আমাদেরও একটু জেনে নিতে হবে কৃষ্ণবস্তু ও তার বিকিরণ সম্মন্ধে।
সাধারণত কোনো বস্তুর তাপমাত্রার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তার থেকে কোনো বিকিরণ হলে, তাকে আমরা বলি তাপীয় বিকিরণ। মজার ব্যাপার হল, এই বিকিরণ শূন্য কেলভিন (-২৭৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস) তাপমাত্রার উপরের যে কোনো তাপমাত্রাতেই হবে এবং যে কোনো বস্তু থেকেই হবে : আমি, তুমি, গাছ, ফুলদানি সবাই এই তাপীয় বিকিরণের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। তবে শুধু বিকিরণই নয়, একই সঙ্গে চলবে আশেপাশের পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ ক্রিয়াও। যখন একটা বস্তুর তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিকের থেকে বেশি হবে, তার বিকিরণের হার শোষণের হারের থেকে বেড়ে যাবে। উল্টোদিকে, বস্তুটির তাপমাত্রা তার পারিপার্শ্বিকের থেকে কম হলে শোষণের হার বিকিরণ হারের থেকে বেশি থাকবে। আর যদি বস্তু ও পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রা সমান হয়? বিকিরণ ও শোষণের সেয়ানে-সেয়ানে টক্করে কেউ একে অপরকে জিততে দেবে না; দু’জনেই নিজের কাজ করে যাবে, ফলস্বরূপ বিকিরণ ও শোষণের হার হবে সমান। এই অবস্থাকে বলে তাপীয় সাম্যাবস্থা। তবে আপাতত একটু বিকিরণের গল্পেই মন দেব আমরা।
একটা জ্বলন্ত মোমবাতিকে আমরা অন্ধকার ঘরে আলোকিত অবস্থায় দেখতে পেলেও ফুটবলকে দেখতে পাই না। কারণ, আলো ফুটবল থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখে এলেই তবে আমরা সেটাকে দেখতে পাব। অন্ধকার ঘরে আলোর অনুপস্থিতিতে ফুটবলও তাই অদৃশ্য। অথচ কি আশ্চর্য ! ফুটবলও তাপীয় বিকিরণ করছে সবসময়। তাহলে কেন আমরা এই বিকিরণ চোখে দেখতে পাই না? উত্তরটা আসলে খুব সহজ। আমরা যে আলো বা তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গকে চোখে দেখতে পাই তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য মোটামুটি ৩৮০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটারের গন্ডীর মধ্যে (তরঙ্গদৈর্ঘ্য : একটি তরঙ্গ একবার কম্পনে যে দূরত্ব অতিক্রম করে)। এর থেকে বেশি বা কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ‘আলো’ আমরা কখনই চোখে দেখতে পাই না। বেশির ভাগ সময়ে এই তাপীয় বিকিরণ দৃশ্যমান আলোর ঘেরাটোপের বাইরে থাকায় আমাদের চোখের নাগালে সে অধরাই থেকে যায়।
একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক। একটা লোহার টুকরো সাধারণ তাপমাত্রায় স্বয়ংপ্রভ নয়। কিন্তু এই লোহাকেই ক্রমশঃ গরম করতে থাকলে তার থেকে আমরা প্রথমে একটা হালকা লাল আভা পাব। এরপর আরো তাপমাত্রা বাড়ালে উজ্জ্বল লাল ও অতি উচ্চ তাপমাত্রায় নীলাভ সাদা রঙের আলো দেখতে পাব। অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোও এই বিকিরণে অংশ নিচ্ছে। যদিও দেখা গেছে, তাপীয় বিকিরণের ক্ষেত্রে কয়েক হাজার কেলভিন তাপমাত্রাতেও দৃশ্যমান আলোর ভাগ মেরেকেটে দশ শতাংশ, বেশিরভাগটাই অপেক্ষাকৃত কম শক্তি বিশিষ্ট অবলোহিত (ইনফ্রারেড) রশ্মি।
তবে এই সব যে বস্তুদের কথা এতক্ষণ বললাম, তারা কিন্তু একটু নাক উঁচু প্রকৃতির। এরা কখনোই সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চুম্বকীয় ‘আলো’র বিকিরণ ও শোষণ করে না। শুধুমাত্র এক রকম বস্তুর হদিশই আমরা জানি, যারা মহান দানীর মত উদার হয়ে সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো যেমন বিকিরণ করতে পারে, আবার সর্বভুকের মত সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকে গিলে নিতেও সক্ষম। ঘরের তাপমাত্রায় এদের উপর আলো পড়লে তা আর প্রতিফলিত হয়ে ফিরতে পারে না; ফলতঃ বস্তুটিকে কালো দেখতে লাগে (ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় এর থেকে আসা বিকিরণও আমাদের চোখে পড়বে না, কারণ তা মূলত অবলোহিত রশ্মি)। এই ধরণের বস্তুকে আমরা কৃষ্ণবস্তু বলে চিনি। ১৮৬০ সালে জার্মান পদার্থবিদ কিরশফের দেওয়া নাম ‘ব্ল্যাকবডি’ই আমাদের ‘কৃষ্ণবস্তু’।
যেহেতু এদের বিকিরণে সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোই অংশগ্রহণ করে, তাই এই কৃষ্ণবস্তুকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাপমাত্রার সঙ্গে বিকিরণের সম্পর্ক সম্মন্ধে সম্যক ধারণা করা সম্ভব। ঊনবিংশ শতকের শেষের তিনটে দশকে জোসেফ স্টিফান, বোলৎজম্যান প্রমুখ খ্যাতনামা পদার্থবিদদের হাত ধরে আমরা তাপীয় বিকিরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পেতে শুরু করেছি। ততদিনে আমরা জেনে গেছি যে, এই বিকিরণ কয়েকটা নিয়ম মেনে চলে। প্রথমত, কৃষ্ণবস্তুটি কি উপাদান দিয়ে তৈরি তা খুব একটা পাত্তা পায় না এই জাতীয় বিকিরণে; একমাত্র তাপমাত্রাই এই বিকিরণের নির্ণায়ক। অন্যদিকে দেখা গেল, একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যে কোনো একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো যে পরিমানে বিকিরিত হচ্ছে, তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে সেই বিকিরণের পরিমান যে সবসময় বাড়তেই থাকবে, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। কিন্তু মুশকিলটা হল, এই বিকিরণের হিসেবগুলো আগের চেনা জানা অঙ্কগুলো দিয়ে ঠিকঠাক মিললো না। জার্মান পদার্থবিদ ডাব্লিউ. য়্যুইন একটা সূত্র দিলেন বটে, কিন্তু তা ছোট তরঙ্গদর্ঘ্যের(উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট) ক্ষেত্রে কাজ করলেও বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণকে(নিম্ন শক্তি বিশিষ্ট) ব্যাখ্যা করতে পারল না। এমনকি ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী লর্ড র্যালে এবং স্যার জেমস জিন্স যে তত্ত্ব দিলেন, তাতে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণকে ব্যাখ্যা করা গেলেও, ছোট তরঙ্গদর্ঘ্যের বেলায় হিসেবে পুরো গোলমাল হয়ে গেল। যেহেতু উচ্চ শক্তিবিশিষ্ট অতিবেগুনী রশ্মির এলাকায় র্যালে-জিন্সের সূত্রের এই ভুলটা ধরা পড়ল, ১৯১১ সালে এই অসামঞ্জস্য অতিবেগুনী বিপর্যয় (আল্ট্রাভায়োলেট ক্যাটাস্ট্রপি) নামে চিহ্নিত হল। মোটের উপর, কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের সম্পূর্ণ ছবি সনাতন বিজ্ঞান দিতে পারলো না। সব চেষ্টাগুলোই অনেকটা অন্ধের হস্তী দর্শনের মত হল; কেউ দেখলেন হাতির লেজ, কেউ বা শুড়। য়্যুইন এবং র্যালে-জিন্সের তত্ত্ব বিকিরণ বর্নালীর দুই বিপরীত প্রান্তের ছবি দিতে পারলেও পুরো ‘হস্তী দর্শন’ সম্ভব হল না।
এদিকে, এই ‘বিপর্যয়’এর খানিকটা আগেই, আনুমানিক ১৮৯৪ সাল নাগাদ ম্যাক্স প্লাঙ্কের নজর পড়েছিল কৃষ্ণবস্তু বিকিরণের অঙ্কটার দিকে। প্রথমে উনি য়্যুইনের কাজের ভিত্তিতেই ১৮৯৯ সাল নাগাদ একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তা সফল হল না। এর পরেই সেই ১৯০০ সালের ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আমাদের আজকের গল্প।
ঠিক যেমন করে একটা ঠান্ডা মাথার মানুষকে একটু একটু করে রাগিয়ে দিলে সে রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে, তার শরীরে চলে আসে আসুরিক বল, তেমন ভাবেই তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবস্তুর পরমাণুগুলোর কাঁপুনিও বাড়তে থাকে, এমনি ছিল ধারণা। এতদিন মনে করা হত, তাপমাত্রা বাড়লে সেই অনুপাতে বস্তুর কাঁপুনি (যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় কম্পাঙ্ক দিয়ে প্রকাশ করা হয়) এবং শক্তি বাড়বে বটে, কিন্তু তা একদমই নিরবচ্ছিন্ন(কনটিনিউআস) ভাবে। সেই যুক্তিকে সমূলে উৎখাত করে প্লাঙ্ক বললেন, শক্তির একটা মৌলিক এবং নূন্যতম একক আছে। যে কোনো পরিমান শক্তি আসলে সেই একক (E) বা তার গুণিতকের সমান(E,২E,৩E ইত্যাদি)। প্লাঙ্ক বললেন, এই ‘E’ পরিমান শক্তিটি কম্পাঙ্কের সঙ্গে সমানুপাতিক। (কম্পাঙ্ক : এক সেকেন্ডে একটি তরঙ্গ যতবার কম্পিত হয়। আবার আমরা জানি, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য একে অপরের সাথে ব্যাস্তানুপাতিক। একটা বাড়লে অন্যটা কমে যায়।) শক্তির সঙ্গে কম্পাঙ্কের সমীকরণ স্থাপন করতে গিয়ে প্লাঙ্ক একটি ধ্রুবকের অবতারণা করলেন। আমরা পেয়ে গেলাম প্লাঙ্ক ধ্রুবককে(h)। ‘E’ কে প্রকাশ করা হল কম্পাঙ্ক এবং ‘h’ এর গুণফল হিসেবে। এই ‘E’ই হল শক্তির ক্ষুদ্রতম একক বা ‘কোয়ান্টাম’। ভবিষ্যতে আইনস্টাইনের হাত ধরে এই ‘E’ কে আবার আমরা অন্য ভাবে চিনবো। তবে সে গল্প পরের পর্বের জন্যই তোলা থাক।
আপাতত আমরা ১৯০০ সালে বসে। সেখানে আমরা দেখছি, অঙ্ক করে যা পাওয়া গেল, নিজেই সেটার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পেতে হিমশিম খাচ্ছেন স্বয়ং প্লাঙ্ক। অতএব আমাদের মত চুনোপুঁটিকে এই মৌলিক একক বা ‘কোয়ান্টাম’-এর ব্যাপারটা বুঝতে একটু বেগ পেতে হবে বৈকি। একটু সহজ করে বোঝার চেষ্টা করি। একটা দড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে গেলে আমরা দড়ির যে কোনো জায়গায় পা রাখতে পারি। কিন্তু একটা মইয়ের ক্ষেত্রে কি তা সম্ভব? একটা মইয়ে এক নম্বর ধাপের পর দু’নম্বর ধাপে আমরা উঠতে পারি, কিন্তু দু’টো ধাপের মধ্যিখানের জায়গাটায় পা ফেলা সম্ভব নয়। সেরকমই শক্তির মইয়ে এক একটা ধাপ ‘E’ বা তার গুনীতকের সমান, এবং শুধুমাত্র সেই ধাপগুলোতেই আমরা শক্তির মান পাব। এতদিনের সনাতনী বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছিল, শক্তির দড়িতে যে কোনও জায়গায় মর্জি মতো পা রাখা সম্ভব, কিন্তু প্লাঙ্কই প্রথম বোঝালেন, শক্তি আদতে দড়ির মত নিরবচ্ছিন্ন (কনটিনিউআস) নয়, মইয়ের ধাপের মত বিযুক্ত(ডিসক্রিট)।
সেদিন ডি.পি.জি.র সম্মেলনে প্লাঙ্কের ‘অদ্ভুত’ অঙ্ক অধিকাংশ বিজ্ঞানীর পুরনো বিশ্বাসকে টলাতে পারল না। ১৯০১ সালে গবেষণাপত্রটি ছাপলো বটে, তবু এর পেছনের তত্ত্বটা তখনো ঠিকমতো বোধগম্য হল না। এমনকি, অতিবেগুনী বিপর্যয়ের গল্পও কিন্তু ১৯০১ সালের পরের ঘটনা, যার অবলম্বন সেই পুরনো সনাতন বিজ্ঞানের ধারণাই। অথচ, যে হস্তী দর্শন আমরা করতে চাইছিলাম এত দিন, পুরোটাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছিল প্লাঙ্কের কষা অঙ্ক দিয়েই, র্যালে-জিন্সের আগেই।
আরও মজার ব্যাপার, প্লাঙ্কের সূত্র থেকে আমরা য়্যুইন এবং র্যালে-জিন্স প্রদত্ত সূত্রেও উপনীত হতে পারলাম। কিন্তু আগেই বলেছিলাম, প্লাঙ্কের এই সাফল্যকে বোঝার জন্য আমাদের ১৯০০ সালের পরেও বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। অপেক্ষা করতে হয়েছে বিজ্ঞানের আরও কিছু ফাঁকফোকরের সন্ধান পাওয়ার জন্য, যা কিছুতেই পুরনো ধারণা দিয়ে মেরামত করা সম্ভব হচ্ছিল না। পুরনো তত্ত্বগুলোর অসাফল্যই পরবর্তী কালে এই ‘E’ এবং ‘h’এর মহিমা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। দেখাবে প্লাঙ্কের সূত্রের সত্যতা। এমনকি আমরা দেখবো, ১৯২৫-এর পর সত্যেন্দ্রনাথ বোস ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রদত্ত পরিসংখ্যানও (বি.ই. স্ট্যাটিসটিক্স) প্লাঙ্কের এই সূত্রকে সীলমোহর লাগিয়ে দেবে। তবে সেই গল্পগুলো নয় পরের পর্বগুলোর জন্যই তোলা থাক।
এলেবেলের দলবল
► লেখা ভাল লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন, আর সকলের সাথে শেয়ার করে সকলকে পড়ার সুযোগ করে দিন।
► এলেবেলেকে ফলো করুন।