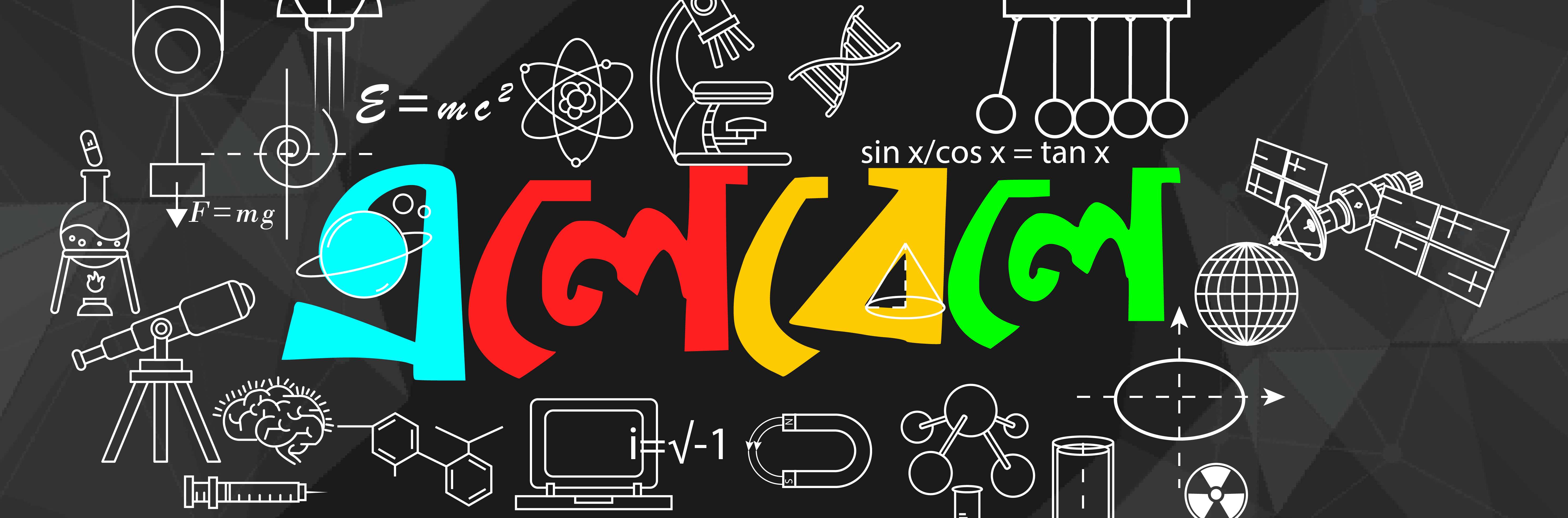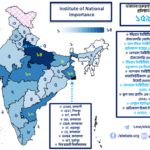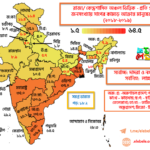~ কলমে এলেবেলের অতিথি অনিরুদ্ধ শাসমল ~
“করোনার টিকা বিজ্ঞানীদের হাতের মুঠোয়””- প্রায়শই খবরের শিরোনামে দেখতে পাওয়া কথাটার পিছনে ঠিক কতটা দীর্ঘ ও কেমন জটিল ভুল-ভুলাইয়া লুকিয়ে আছে- আমাদের আজকের আলোচনা তাই নিয়ে। তবে করোনার টিকা নয়, আমাদের আলোচ্য সার্বিকভাবে টিকা বা ভ্যাকসিন গবেষণা, তার পরীক্ষামূলক ব্যবহার ও তার উৎপাদন পর্যায়গুলি।
ব্যাপারটা যদিও সবার জানা, তবু একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক -টিকা আর ওষুধের মূল ফারাকটা কি। সাধারণত টিকা হলো আগাম কোন রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে শরীরে প্রতিষেধক বীজ বা তার খন্ডাংশ প্রয়োগ করে শরীরকে আগাম রোগ-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত রাখা। অন্যদিকে ওষুধ হলো রোগ-আক্রমণের পর তার বিরুদ্ধে লড়াই করার হাতিয়ার। সেই অর্থে টিকা হল রোগের বিরুদ্ধে একটা দুর্গের মত আর ওষুধ হলো রিজার্ভে থাকা সেনাবাহিনী। এখন এই টিকার গবেষণা, পরীক্ষামূলক ব্যবহার এবং জনসাধারণের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত যে পর্ব-পর্যায়গুলো অনুসরণ করা হয় সেগুলোকে সরল আকারে পরিবেশন করা যাক। যেকোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতই এক্ষেত্রেও সমস্ত রকম পর্ব-পর্যায় খুব একটা সরলভাবে এবং ক্রমানুযায়ী অনুসরণ করা হয় না। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে নিখাদ গবেষণাধর্মী কার্যকলাপের পাশাপাশি বাণিজ্যিক দিকটাও মাথায় রাখা হয়।
রোগ জরিপ পর্ব (ক্লিনিক্যাল সার্ভে): ভ্যাকসিন প্রস্তুতের একদম শুরুটাই হয় ক্লিনিক্যাল সার্ভে দিয়ে। এই সার্ভেতে দেখে নেওয়া হয় কোনো রোগের ভয়াবহতা এবং তার সঙ্গে জড়িত জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক ক্ষতির হিসাব। কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়ে থাকে, যেমন রোগ সংক্রমণের হার কত এবং সংক্রমিত হলে মৃত্যুহার খুব বেশি কিনা (যেমন ডিপথেরিয়া), রোগ থেকে দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় কিনা (যেমন পোলিও), রোগ সংক্রমণে পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা কেমন (যেমন কলেরা), এবং সবথেকে যে বিষয়ের উপর বেশি জোর দেয়া হয় সেটা হলো প্রসূতি ও শিশু-সংক্রমণ এবং মৃত্যুহার খুব বেশি কিনা (যেমন হাম)। এই সব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ভ্যাকসিন প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় সংক্রমিত মানুষের থেকে জীবাণুর নমুনা (ক্লিনিক্যাল আইসোলেট) সংগ্রহ করা। এইভাবে একটা সুবিশাল নমুনার (ন্যূনতম কয়েক হাজার) লাইব্রেরী তৈরি করে তার মধ্যে জীবাণুর প্রকারভেদ (Serotype detection বা Genetic profiling এর মাধ্যমে) ও তার মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী কয়েকটি সংক্রমণকারী প্রকারভেদকে চিহ্নিত করা হয়। এই পর্বে বাছাই করা জীবাণুর প্রকারভেদের আরও গভীর চরিত্র বিশ্লেষণের পর সেগুলো পরবর্তী পর্বের জন্য পাঠানো হয়।
অনুসন্ধানমূলক গবেষণা পর্ব (discovery/exploratory research): এই পর্বে বিস্তর গবেষণার মাধ্যমে ঠিক করা হয় টিকার বীজ (Antigen) কি এবং শরীরকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে রোগপ্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তোলা হবে। এখনো পর্যন্ত মানব শরীরে প্রয়োগের জন্য যে ক’টি সফল ভ্যাকসিন চালু আছে সেগুলি মূলত চারটি প্রকারে প্রস্তুত করে শরীরে প্রয়োগ করা হয়-
১) জীবিত অথচ সংক্রমণে অক্ষম (Live attenuated) জীবাণু- MMR ভ্যাকসিন, ওর্যাল পোলিও ভ্যাকসিন ।
২) সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বা মৃত জীবাণু (Inactivated)- জলাতঙ্ক ভ্যাকসিন।
৩) জীবাণুর নিষ্ক্রিয় বিষ (Toxoid)- টিটেনাস ভ্যাকসিন।
৪) জীবাণুর খন্ডাংশ (Subunit) – এই খন্ডাংশ জীবাণুর নানা রকম জৈব পদার্থ ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়। যেমন হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন এর জন্য জীবাণুর প্রোটিন, নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন এর জন্য জীবাণুর শর্করা প্রলেপ এবং হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV) ভ্যাকসিন এর জন্য জীবাণুর বাইরের আবরণ (Capsid) কে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অনুসন্ধানমূলক গবেষণার পর্যায়ে এক বা একাধিক মাধ্যম অনুসরণ করে সবথেকে উপযুক্ত এবং কার্যকরী টিকা-বীজ নির্ণয় করা হয়। তারপর শুরু হয় টিকাবীজের ঘষামাজা, যাতে করে তা শরীরে অনাক্রম্যতা বাড়াতে বেশী কার্যকরী হয়। যেমন শর্করাজাতীয় অ্যান্টিজেন-এর ক্ষেত্রে প্রোটিনের সাথে সংযুক্তি (Conjugation) বা প্রোটিন জাতীয় অ্যান্টিজেন-এর ক্ষেত্রে তার ত্রিমাত্রিক আকারের সামান্য পরিবর্তন (Configurational change)- এইসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অনুসন্ধানমূলক গবেষণাস্তরে মোটামুটি সময় লাগে চার থেকে ছয় বছর।
প্রিক্লিনিক্যাল পর্ব: এই পর্বে পরীক্ষামুলকভাবে টিকার কার্যকারিতা দেখা হয় গবেষণাগারে কৃত্রিম ভাবে লালিত বিভিন্ন কোষ ও কলা নমুনাতে এবং বিভিন্ন মনুষ্যেতর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে প্রয়োগ করে। ইঁদুর/গিনিপিগের মত ছোট প্রাণীর ওপর প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে অনাক্রম্যতা বৃদ্ধি পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োগ সফল হলে, বাঁদর প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে তার নিরাপদ মাত্রা, অনাক্রম্যতা বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাই করা হয়। এছাড়াও, এই পর্বে ভ্যাকসিনের প্রস্তুতি সূত্রটিও (Formulation) নির্ধারণ করা হয়। ভ্যাকসিনের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব বজায় রাখতে এবং শরীরে অনাক্রম্যতা বৃদ্ধির হার উন্নত করার জন্য নানা রকমের স্থিতিকারক পদার্থ (Stabilizer), অনাক্রম্যতা সহায়ক (Adjuvant) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এই পর্বে ভ্যাকসিন প্রদানের সব থেকে কার্যকর প্রণালী (ইনজেকশনের মাধ্যমে বা খাবারের মাধ্যমে) সুনিশ্চিত করা হয়। প্রিক্লিনিক্যাল পর্ব এক থেকে দু’বছর পর্যন্ত চলতে থাকে।
পরীক্ষামূলক ব্যবহার পর্ব (ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল):
এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্ব যেহেতু এই পর্বে মানবশরীরের উপর ভ্যাকসিন এর প্রথম পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। স্বভাবতই এই পর্বে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। মূলত চার/পাঁচটি পর্যায়ে এই পর্ব বিভক্ত-
১) শূন্য পর্যায় (Phase 0): এটি একটি ঐচ্ছিক পর্যায়। খুবই কম সংখ্যক (১৫-২০ জন) সুস্থ এবং প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপর কম পরিমাণে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে দেখা হয় তা নিরাপদ কিনা।আজকাল এই পর্যায়টিকে বেশিরভাগ সময় বাদ দেওয়া হয়।
২) প্রথম পর্যায় (Phase 1): এই পর্যায়ে ৩০-১০০ জন সুস্থ এবং প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়। প্রাথমিকভাবে ভ্যাকসিন-এর সর্বোচ্চ নিরাপদ মাত্রা পরীক্ষা করা ছাড়াও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার পরিমাণ এবং টিকাকরণ প্রণালীর উপর বিশেষ নজর দেয়া হয়। ঐতিহাসিকভাবে এই পর্যায়ে সাফল্যের হার মোটামুটি ৭০-৮০ শতাংশ এবং শেষ হতে সময় লাগে এক থেকে দুই বছর।
৩) দ্বিতীয় পর্যায় (Phase 2): দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষাতে কয়েকশো (৩০০-৮০০) মানুষের ওপর ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে মূলতঃ লক্ষ্য করা হয় অনাক্রম্যতার মাত্রা, টিকার নিরাপদ মাত্রা এবং সংবেদনশীল জনগোষ্ঠীতে (High risk population) বয়স-লিঙ্গ-জাতিভেদে প্রতিক্রিয়া কেমন হচ্ছে। শিশুরোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যেসব ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়, এই পর্যায়েই প্রথম সেগুলি পরীক্ষামুলকভাবে বিশেষ কিছু শিশুদের ওপর প্রয়োগ করা হয়, যাদের শরীরে আগে থেকেই অনাক্রম্যতা (High antibody level) তৈরি হয়ে আছে। এই পর্যায়ে ভ্যাকসিনের একাধিক সহায়ক মাত্রা (booster dose) প্রয়োজন হয় কিনা তাও দেখা হয়। এই পর্যায়ে সাফল্যের হার ৪০-৬০ শতাংশ এবং শেষ হতে সময় লাগে দুই থেকে তিন বছর।
৪) তৃতীয় পর্যায় (Phase 3): এই পর্যায়ে এক বিরাট জনসংখ্যার (১ হাজার থেকে ৩০ হাজার পর্যন্ত) উপর ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা ৬০-৭০ হাজার পর্যন্ত হয়। Randomized controlled trial (RCT) বিধি অনুসরণ করে কিছু মানুষকে সত্যিকারের ভ্যাকসিন এবং কিছু মানুষকে অন্য ভ্যাকসিন বা মিছিমিছি ভ্যাকসিন (placebo) দিয়ে দেখা হয় সমষ্টিগত টিকার প্রভাব, প্রতিরোধ ক্ষমতা, এবং জীবাণুর পুনঃ- প্রাদুর্ভাব। এই পর্যায়ে ও সাফল্যের হার ৬০-৭০ শতাংশ এবং এই পর্যায় শেষ হতে চার বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। সব মিলিয়ে একটা ভ্যাকসিনের সম্পূর্ণ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে সাফল্যের হার ৩০-৩৫ শতাংশ। তৃতীয় পর্যায়ে সাফল্য পেলে তবেই সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার (Regulatory body) কাছ থেকে অনুমোদনের আবেদন করা যায়।
৫) চতুর্থ পর্যায় (Phase 4): বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুমোদিত টিকা জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার পরও বিজ্ঞানীদের নজর থাকে টিকার কার্যক্ষমতা, গোষ্ঠী অনাক্রম্যতা এবং জীবানুর চরিত্র বদল এর উপর। এই পর্যায় চলতে থাকে দীর্ঘদিন ধরে এবং ব্যাপক সংখ্যায় নমুনা সংগ্রহ চলতে থাকে যেগুলি ভবিষ্যতে আরও উন্নত এবং কার্যকরী ভ্যাকসিন তৈরিতে সাহায্য করে।
অনুমোদন পর্ব (Regulatory approval): ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সব তথ্য সংগৃহীত হলে সেগুলি টিকা প্রস্তুতকারি সংস্থা এবং স্বতন্ত্র কোন সংস্থা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক)। এরপর এই দুই স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষিত তথ্যরাশি সংশ্লিষ্ট জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে পেশ করতে হয়। আধুনিক ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তা কাজ করছে (নিরাপদ এবং অনাক্রম্যতা বৃদ্ধি) তা দেখালেই হয়না, ছাড়পত্র পেতে গেলে কোন পদ্ধতিতে (Mechanism of action) টিকা মানব শরীরে কাজ করছে তাও বিস্তারিতভাবে গবেষণা করে জানাতে হয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে এই নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে টিকা প্রস্তুত করার একদম প্রাথমিক পর্যায় থেকে সবকিছু বিস্তারিত জানানো হতে থাকে।
উৎপাদন পর্ব: এতদুর পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক চললে তারপর শুরু হয় বৃহৎ আকারে উৎপাদন প্রক্রিয়া। ব্যাপারটা অনেক বেশি জটিল, পরিশ্রম- ও খরচ- সাপেক্ষ। ভ্যাকসিনের এক একটি ব্যাচ উৎপাদন করতে তিন থেকে ৩৬ মাস পর্যন্ত সময় লাগে। ভ্যাকসিন তৈরীর কাঁচামাল হিসেবে জৈব মিশ্রণের (মাইক্রোবিয়াল কালচার) যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চমানের কারিগরি দক্ষতা এবং নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। যেহেতু ভ্যাকসিনের বিশুদ্ধতা মানব স্বাস্থ্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে তাই ভ্যাকসিন উৎপাদনের ৫০-৬০ শতাংশ সময় ব্যয় করা হয় গুণমান নিয়ন্ত্রণের (Quality control) জন্য। এরপর যথাযথ প্যাকেজিং ব্যবস্থা (তাপমাত্রা খুব গুরুত্বপূর্ণ) করে তা দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হয় বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের কাছে।
তাহলে মোট কত সময় লাগে একটা টিকা আবিষ্কার ও তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে? গড়ে ১০-১২ বছর। তাহলে আমরা কিভাবে আশা করছি যে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই চলে আসবে। একটা বড় কারণ হল, এই আপদকালীন পরিস্থিতিতে প্রচুর গবেষক এবং চিকিৎসকদের নিরলস প্রচেষ্টা। এছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষামূলক ব্যবহার পর্যায়গুলি সমান্তরালভাবে পরিচালনা করার ফলেও কিছুটা সময় বেঁচেছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার কিছু নিয়মকানুন শিথিল করা হয়েছে, যদিও তাতে ভ্যাকসিনের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনরকম আপোষ করা হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে আরেকটা ব্যাপার আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে করোনার ভ্যাকসিন অনুমোদন হয়ে যাওয়ার পরেও অন্তত দুই থেকে তিন বছর লাগবে সেটা পৃথিবীর সব মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। তাই ততদিন মাস্ক ব্যবহার করুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন এবং সুস্থ থাকুন।
অনিরুদ্ধ নিউ ইয়র্কে ফাইজার (Pfizer) ভ্যাকসিন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেণ্টে কর্মরত বিজ্ঞানী।
► লেখা ভাল লাগলে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন, আর সকলের সাথে শেয়ার করে সকলকে পড়ার সুযোগ করে দিন।
► এলেবেলেকে ফলো করুন।